Untitled
- Milu Tution Center
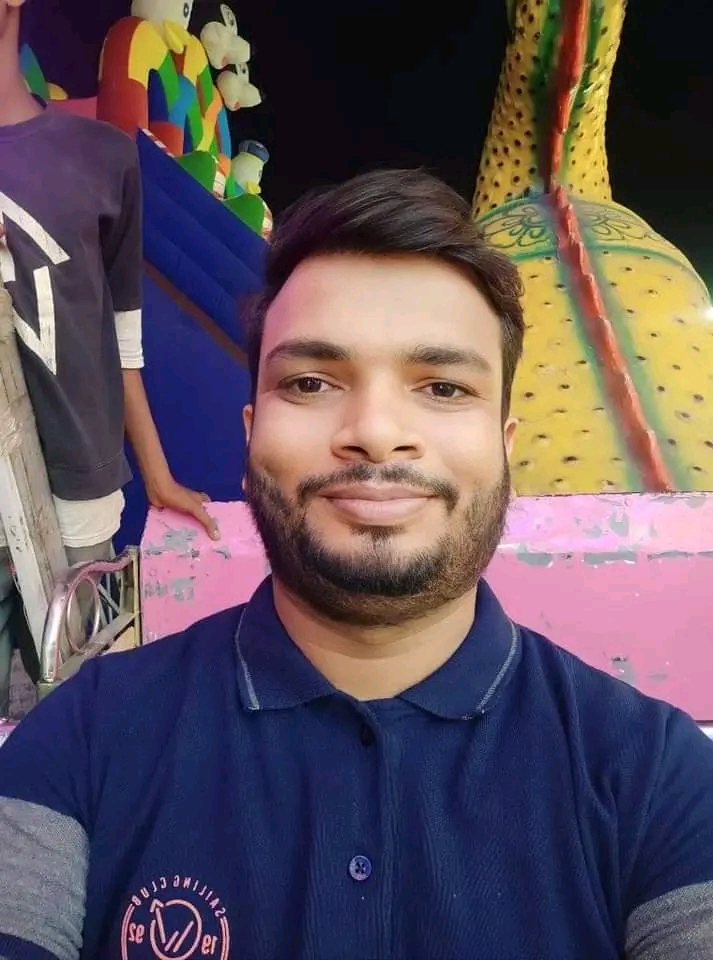
- Mar 12, 2021
- 23 min read
নদী, হিমবাহ, বায়ুর কাজ (বিস্তারিত) ২
-02 নদীর কাজ নদীর পুনর্যৌবনলাভ (REJUVENATION) ও নিক পয়েন্ট (KNICK POINT): ☻নদীর পুনর্যৌবনলাভ (Rejuvenation): সংজ্ঞাঃ একটি ক্ষয়চক্র সম্পুর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শেষ পর্যায়ে পৌছাবার আগেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটলে বা সমুদ্রজলতলের পরিবর্তন ঘটলে নদীঢালের সামঞ্জস্য নষ্ট হয় । এর ফলে নদী তার ঢালের সামঞ্জস্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য নতুনভাবে তার ক্ষয়কার্য দ্রুত গতিতে শুরু করে অর্থাৎ নদী তার বার্ধক্য অবস্থা থেকে পুনরায় যৌবন অবস্থাপ্রাপ্ত হয় । একে নদীর পুনর্যৌবনলাভ (Rejuvenation) বলে । উদাঃ ভূমধ্যসাগরের জলতল নেমে যাওয়ার কারণে নীল নদের পুনর্যৌবনলাভ এবিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বৈশিষ্ট্যঃ নদীর পুনর্যৌবনলাভ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) পুনর্যৌবনলাভের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূমিরূপগুলিকে নদী পুনরায় তার কার্য দ্বারা প্রভাবিত করতে থাকে । খ) এর ফলে একটি নতুন ক্ষয়চক্রের সূচনা হয় । গ) উপত্যকা গঠনের কাজ আবার নতুনভাবে শুরু হয় । ঘ) নদী তার নদীবক্ষকে গভীরভাবে কর্তন করে ও পুরানো নদী উপত্যকা নদীর দুপাশে ধাপ সৃষ্টি করে নদীমঞ্চরূপে অবস্থান করে । সৃষ্টির কারণ বা নিয়ন্ত্রকসমূহঃ নদীর পুনর্যৌবনলাভ সৃষ্টির কারণ বা নিয়ন্ত্রকগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) ভূ-আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উত্থান বা সমুদ্র-গহ্বরের অবনমন, খ) সমুদ্রের অপসারণ, গ) জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীতে জলের পরিমান বৃদ্ধি, ঘ) একটি নদীগোষ্ঠীর অপর নদীগোষ্ঠীতে আত্মসমর্পন ও নদীগোষ্ঠীর পূনর্বিন্যাস, ঙ) নদীর বোঝা হ্রাস প্রভৃতি । সৃষ্ট ভূমিরূপঃ নদীর পুনর্যৌবনলাভের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি হলো – ক) পূনর্গঠিত উপত্যকা, খ) নিক পয়েন্ট, গ) নদীমঞ্চ বা নদীসোপান, ঘ) কর্তিত নদীবাঁক, ঙ) স্বাভাবিক সেতু, চ) জলপ্রপাত প্রভৃতি । শ্রেণীবিভাগঃ নদীর পুনর্যৌবনলাভ মূলত তিনপ্রকার । যথা – ক) গতিজনিত পুনর্যৌবনলাভ (Dynamic Rejuvenation): ভূ-আন্দোলনের ফলে নদী অববাহিকাসংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগ কাত হয়ে বা হেলে পড়লে অথবা অথবা চ্যুতি দ্বারা প্রভাবিত হলে নদীর ঢাল অনেকসময় অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় । ফলস্বরূপ নদী পুনর্যৌবনলাভ করে এবং তার নিম্নক্ষয় ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় । একে নদীর গতিজনিত পুনর্যৌবনলাভ (Dynamic Rejuvenation) বলে । খ) স্থিতিজনিত পুনর্যৌবনলাভ (Static Rejuvenation): ভূ-আন্দোলনজনিত কোনপ্রকার উত্থান-পতন ছাড়াই নদীর বোঝা হ্রাস, নদীতে জলপ্রবাহের পরিমান বৃদ্ধি, নদীগোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি কারণে স্থিতিশীল ভূ-পৃষ্ঠস্থ নদীর পুনর্যৌবনলাভ হলে তাকে স্থিতিজনিত পুনর্যৌবনলাভ (Static Rejuvenation) বলে । গ) সমুদ্রতলজনিত পুনর্যৌবনলাভ (Eustatic Rejuvenation): সমুদ্র-গহ্বরের ধারণ ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে অথবা মহাদেশীয় হিমবাহের দ্বারা সমুদ্রজলতলের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে । এমতাবস্থায়, নদী পুনরায় তার প্রবাহে যৌবনাবস্থা লাভ কলে তাকে সমুদ্রতলজনিত পুনর্যৌবনলাভ (Eustatic Rejuvenation) বলে । ☻নিক পয়েন্ট (Knick Point):সংজ্ঞাঃ ক্ষয়চক্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যায়ে পৌছাবার আগেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটলে বা সমুদ্রজলতলের পরিবর্তন ঘটলে নদীঢালের সামঞ্জস্য নষ্ট হয় । এর ফলে নদী তার ঢালের সামঞ্জস্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য নতুনভাবে তার ক্ষয়কার্য দ্রুত গতিতে শুরু করে । এই নতুন ঢাল ও পুরানো ঢাল মিলনস্থলে একটি খাঁজ সৃষ্টি হয় । এই খাঁজকেই নিক পয়েন্ট (Knick Point) বলে । নিক পয়েন্ট (Knick Point) উদাঃ কাঞ্চি নদীতে নিক পয়েন্ট দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ নিক পয়েন্ট (Knick Point) – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) নিক পয়েন্ট ঢালের পার্থক্যকে নির্দেশ করে । খ) সাধারণতঃ নিক পয়েন্টে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় । [নদীর প্রবাহপথে তার ঢালের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হলে নদী তা ফিরিয়ে আনবার জন্য পুনরায় মস্তকের দিকে নতুন খাঁত কেটে অগ্রসর হয় এবং ঐ নতুন ঢাল ও পুরানো ঢাল যেখানে মিলিত হয় সেই স্থানে ঢালজনিত পার্থক্যের জন্য নদীর জলধারা উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে জলপ্রপাত সৃষ্টি করে । এই কারণে অধিকাংশ নিক পয়েন্টেই জলপ্রপাত সৃষ্টি হতে দেখা যায় ।] গ) নদী অববাহিকার উত্থান বা সমুদ্র-গহ্বরের অবনমন, সমুদ্রের অপসারণ, নদীতে জলের পরিমান বৃদ্ধি, নদীগোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি কারণে নদীতে ঢালের পার্থক্য সৃষ্টি হলে নিক পয়েন্ট সৃষ্টি হয় । ঘ) সময়ের সাথে সাথে এটি ক্রমশ মস্তকের দিকে সরে যেতে থাকে এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে পর্যায়িত ঢালে পরিনত হয় । নদীমঞ্চ বা নদীসোপান (RIVER TERRACE): ☻সংজ্ঞাঃ নদী উপত্যকার দুই তীর ধাপে ধাপে নেমে এসে নদীর দুই পাশে মঞ্চের মত অবস্থান করলে তাকে নদীমঞ্চ বা নদীসোপান (River Terrace) বলে । উদাঃ গঙ্গা, তিস্তা, ব্রক্ষ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীতে এরূপ নদীমঞ্চ দেখা যায় । নদীমঞ্চ বা নদীসোপান (River Terrace) উৎপত্তিঃ স্থলভাগ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্যের জন্য নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর পার্শ্বচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আড়াআড়িভাবে গঠিত পার্শ্বচিত্রেরও অর্থাৎ নদী উপত্যকারও পরিবর্তন হয় । নদী উপত্যকা সরু থেকে ক্রমশ চওড়া হয়ে প্রবীণত্ব লাভ করে । কিন্তু স্থলভাগ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্যের ফলে নদী পুনর্যৌবন লাভ করে তার প্রবীণ উপত্যকাকে পুনরায় কর্তিত করতে থাকে । ফলে নদীর নতুন উপত্যকা প্রবীণ উপত্যকা অপেক্ষা অধিক গভীর হয় এবং ঐ প্রবীণ উপত্যকা নতুন উপত্যকার দুই তীরে মঞ্চের মত অবস্থান করতে থাকে । সময়ের সাথে সাথে একাধিকবার নদীর পুনর্যৌবনলাভ হলে নদীর দুই তীরে একাধিক ধাপবিশিষ্ট নদীমঞ্চ সৃষ্টি হয় । বৈশিষ্ট্যঃ নদীমঞ্চ বা নদীসোপান – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ – ক) একটি নদী উপত্যকায় একাধিক নদীমঞ্চ দেখা যায় । খ) নদীতে নদীমঞ্চের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় সেই অঞ্চলটি মোট কতবার উন্নত (Uplift) হয়েছে । খাঁড়ি (ESTUARY / FIRTH): ☻সংজ্ঞাঃ নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থলে নদীর মোহনা যথেষ্ট গভীর, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত আকৃতিবিশিষ্ট হলে তাকে খাঁড়ি (Estuary / Firth) বলে । উদাঃ ওব নদীর মোহনাসংশ্লিষ্ট খাঁড়িটি পৃথিবীর দীর্ঘতম খাঁড়ি । এছাড়াও আমাজন, টেমস, ফোর্থ প্রভৃতি নদীর খাঁড়িও পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাঁড়ির উদাহরণ । উৎপত্তিঃ মোহনার নিকট নদীর স্রোত অথবা জোয়ারের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশী হলে নদীবাহিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি মোহনা অঞ্চলে সঞ্চিত হতে পারে না । ফলে জোয়ারের জল প্রবলবেগে নদীর মধ্যে প্রবেশ করে মোহনাসংশ্লিষ্ট নদীখাঁতকে ক্ষয় করে অধিক গভীর ও প্রশস্ত (চ্যাপ্টা বোতল বা ফানেল আকৃতির) করে তুলতে থাকে এবং ক্রমশ খাঁড়ির সৃষ্টি হয় । নিয়ন্ত্রকসমুহঃ একটি আদর্শ খাঁড়ি অঞ্চল সৃষ্টি হওয়ার নিয়ন্ত্রকগুলি হল – ক) নদীর জলপ্রবাহ ও জোয়ারের স্রোতের আপেক্ষিক শক্তির উৎস, খ) নদী মোহনা – র গঠন ও আকৃতি, গ) ড্রেজিং – এর মত কৃত্রিম কারণ প্রভৃতি । বৈশিষ্ট্যঃ খাঁড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ – ক) এটি গভীর, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয় । খ) একটি আদর্শ খাঁড়ি অঞ্চলে ব-দ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় । গ) খাঁড়ির মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জোয়ারের জল নদীতে প্রবেশ করে এবং নদীর মধ্য দিয়ে স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয় । একে বান (Bore) বলে । ঘ) খাঁড়ি অঞ্চল পলিমুক্ত থাকার কারণে পরিস্কার ও গভীর থাকে, ফলে জাহাজ চলাচল সুবিধাজনক হয় । ঙ) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয় । ব-দ্বীপ (DELTA): ☻নামকরণঃ গ্রীক অক্ষর ‘Δ’ (Delta) বা বাংলা অক্ষর মাত্রাহীন ‘ব’ এর থেকে ব-দ্বীপ বা Delta শব্দটি এসেছে । সংজ্ঞাঃ মোহনায় এসে নদীগর্ভে বালি, পলি, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে নদীবক্ষে প্রায় ত্রিকোণাকার ভূমিভাগ গড়ে উঠলে তাকে ব-দ্বীপ (Delta) বলে । ব-দ্বীপ (Delta) উদাঃ গঙ্গা নদী ও ব্রক্ষ্মপুত্র নদের মোহনায় গঠিত মিলিত ব-দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ । পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বেশীরভাগ অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা সুবিশাল এই ব-দ্বীপের আয়তন প্রায় ৭৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার । উৎপত্তিঃ নদীর মোহনায় সুক্ষ্ম পলির সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নদীগর্ভ অধিক পলি সঞ্চয় দ্বারা ভরাট হয়ে উঁচু হয়ে ওঠে । ফলে নদীর গভীরতা কমে যায় । এদিকে ভূমিঢালও একেবারে কমে যাওয়ার ফলে নদীতে স্রোত বিশেষ থাকে না বললেই চলে । এমতাবস্থায় নদীপ্রবাহে সামান্য বাঁধা পেলেই নদী বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয় । নদীর দুই শাখার মধ্যবর্তী অংশে বালি, পলি, কর্দম প্রভৃতির সঞ্চয় ঘটে । সময়ের সাথে সাথে এই সঞ্চয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপ গড়ে ওঠে । আদর্শ ব-দ্বীপ গড়ে ওঠার অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশঃ একটি আদর্শ ব-দ্বীপ গড়ে ওঠার অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বা শর্তগুলি হলো নিম্নরূপ – a) সংশ্লিষ্ট সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত ও তাতে জোয়ারভাটার প্রকোপ কম থাকা প্রয়োজন । b) মোহনাসংশ্লিষ্ট সমুদ্র স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন । c) নদীস্রোতের বিপরীতমুখী জোরালো বায়ুপ্রবাহ থাকা প্রয়োজন । d) নদীটি দীর্ঘ গতিপথবিশিষ্ট এবং তার তিনপ্রকার প্রবাহই (উচ্চপ্রবাহ, মধ্যপ্রবাহ ও নিম্নপ্রবাহ) সুস্পষ্টভাবে থাকা আবশ্যক । e) নদীবাহিত পললরাশির পরিমান অধিক হওয়া প্রয়োজন । f) মোহনার কাছে সমুদ্র অগভীর হওয়া আবশ্যক । g) সমুদ্রের জলে লবনতা বেশী হলে তা ব-দ্বীপ গঠনের পক্ষে সহায়ক হয় । h) মোহনার কাছে সমুদ্রজলের ঘনত্ব বেশী হলে তা ব-দ্বীপ গঠনের পক্ষে আদর্শ হয় । শ্রেণীবিভাগঃ মূলত তিন প্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে ব-দ্বীপকে বিভক্ত করা হয় । যথা – ক) উৎপত্তি অনুযায়ী – ব-দ্বীপ কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে ব-দ্বীপকে মুলত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা – ১. গঠনমূলক ব-দ্বীপঃ আমরা জানি পৃথিবীর অধিকাংশ ব-দ্বীপ নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত হয় । তবুও দেখা যায়, এই জাতীয় ব-দ্বীপ গঠনে সমুদ্রের তরঙ্গ বা জোয়ার-ভাটার প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয় না । কেবলমাত্র নদীর সাথে বয়ে আনা অধিক পলির পরিমানের উপর নির্ভর করেই গঠনমূলক ব-দ্বীপ গড়ে ওঠে । এই শ্রেণীর ব-দ্বীপ মূলত গ্রীক অক্ষর ‘Δ’ (Delta) বা বাংলা অক্ষর মাত্রাহীন ‘ব’ এর মত দেখতে । উদাঃ গঙ্গা, হোয়াংহো, পো, রোন, নীল প্রভৃতি নদ-নদীর মোহনায় গঠিত ব-দ্বীপ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । ২. ক্ষয়ধর্মী ব -দ্বীপঃ জোয়ার-ভাটা এবং সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়কার্যের ফলে যে ব-দ্বীপ গঠিত হয়, তাকে ক্ষয়ধর্মী ব-দ্বীপ বলে । উদাঃ মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । খ) অবস্থান অনুযায়ী – ব-দ্বীপের অবস্থান অনুযায়ী একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা – ১. নদী ব-দ্বীপঃ প্রধান নদীর সাথে যেখানে উপনদী এসে মিলিত হয় সেখানে উপনদী দ্বারা নুড়ি, বালি, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণাকার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় । একে নদী ব-দ্বীপ বলে । উদাঃ দামোদর ও হুগলী নদীর মিলনস্থলে এরকম ব-দ্বীপ দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ নদী ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – a) এইপ্রকার ব-দ্বীপ নদী ও উপনদীর মিলনস্থলে গড়ে ওঠে । b) উপনদীবাহিত পদার্থের পরিমান ও প্রকৃতির উপর নদী ব-দ্বীপের আকৃতি নির্ভর করে । ২. হ্রদ ব-দ্বীপঃ বিশাল হ্রদে অনেকসময় নদী এসে পতিত হয় । এর ফলে নদীবাহিত নুড়ি, বালি, কর্দম প্রভৃতি হ্রদসংলগ্ন নদীমোহনায় জমা হয়ে ব-দ্বীপ গড়ে উঠলে তাকে হ্রদ ব-দ্বীপ বলে । উদাঃ ইউরোপে কাষ্পিয়ান সাগরে পতিত ভলগা নদীর মোহনায় এরূপ একটি সুবিশাল হ্রদ ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে । বৈশিষ্ট্যঃ হ্রদ ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – a) হ্রদের আকার বিশাল হলে এবং নদীবাহিত পদার্থের পরিমান বেশী হলে এরূপ ব-দ্বীপ বিশালাকৃতি হতে পারে । b) হ্রদের জলরাশি অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকার ফলে ব-দ্বীপের সম্মুখভাগ হ্রদতরঙ্গ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় না । এবং ৩. সমুদ্র ব-দ্বীপঃ নদী যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেই অংশকে নদীর মোহনা বলে । এই অংশে নদীর স্রোত সমুদ্রে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় বলে নদীবাহিত যাবতীয় পলি, বালি, কর্দম এই স্থানে জমা হয় এবং ব-দ্বীপ গড়ে ওঠে । একে সমুদ্র ব-দ্বীপ বলে । উদাঃ গঙ্গানদী ও ব্রক্ষ্মপুত্র নদের মোহনায় গঠিত মিলিত ব-দ্বীপ এই প্রকার ব-দ্বীপের উদাহরণ, যেটি আবার পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপও (আয়তন প্রায় ৭৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার) বটে । বৈশিষ্ট্যঃ সমুদ্র ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – a) নদীর স্রোত সমুদ্রে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে এরূপ ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় । b) এইপ্রকার ব-দ্বীপ মূলত স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত ও অপেক্ষাকৃত শান্ত সমুদ্রসংলগ্ন মোহনায় গড়ে ওঠে । গ) আকৃতি অনুযায়ী – আকৃতি অনুযায়ী ব-দ্বীপকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা – ১. ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপঃ প্রধান নদীতে উপনদী এসে মিশলে বা প্রধান নদী থেকে শাখানদী বেরিয়ে গেলে সেই বিশেষ সংযোগস্থলে পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে আয়তন প্রায় ৭৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার সৃষ্টি হয় তা প্রধানত প্রায় তিন কোণা দেখতে হয় বলে একে ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপ বলে । ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপ উদাঃ দামোদর নদ ও হুগলী নদীর সংযোগস্থলে সৃষ্টি হওয়া ব-দ্বীপ । বৈশিষ্ট্যঃ ত্রিকোণাকৃতি ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ a) এই শ্রেণীর ব-দ্বীপ মূলত গ্রীক অক্ষর ‘Δ’ (Delta) বা বাংলা অক্ষর মাত্রাহীন ‘ব’ এর মত দেখতে হয় । b) নদীবাহিত পদার্থের পরিমান ও প্রকৃতির উপর এইপ্রকার ব-দ্বীপের আকৃতি নির্ভর করে । ২. ধনুকাকৃতি ব-দ্বীপ (Arcuate Delta): যে সকল ব-দ্বীপের সমুদ্রমুখী রেখা সমুদ্রের দিকে ধনুকের মত বেঁকে যায়, তাদের ধনুকাকৃতি ব-দ্বীপ(Arcuate Delta) বলে । উদাঃ নীলনদের ব-দ্বীপ, হোয়াংহো নদীর ব-দ্বীপ, রাইন নদীর ব-দ্বীপ প্রভৃতি । ধনুকাকৃতি ব-দ্বীপ (Arcuate Delta) ধনুকাকৃতি ব-দ্বীপ (Arcuate Delta) বৈশিষ্ট্যঃ ধনুকাকৃতি ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – a) এই প্রকার ব-দ্বীপ ভারী পদার্থ যেমন – কাদার স্তর, নুড়ি, বালি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত হয় । b) এই প্রকার ব-দ্বীপ প্রতি বছরই একটু একটু করে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয় বলে এদের বর্ধনশীল ব-দ্বীপও বলা হয় । ৩. পক্ষীপদসদৃশ ব-দ্বীপ বা পাখির পায়ের মত ব-দ্বীপ (Bird-foot Delta): ব-দ্বীপের আকৃতি বিবর্তিত হতে হতে কালক্রমে তা পাখির পায়ের মত আকার ধারণ করলে তাকে পক্ষীপদসদৃশ ব-দ্বীপ বা পাখির পায়ের মত ব-দ্বীপ (Bird-foot Delta) বলে । পক্ষীপদসদৃশ ব-দ্বীপ বা পাখির পায়ের মত ব-দ্বীপ (Bird-foot Delta) উদাঃ মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ । উৎপত্তিঃ নদীবাহিত উপাদানগুলি যদি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও হালকা প্রকৃতির হয় তাহলে প্রধান নদী ও তার শাখানদীগুলি সমুদ্রের অনেক ভিতরে এই সকল উপাদান গুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে বিভিন্নদিকে সঞ্চয় করে । প্রধান নদী ও তার শাখানদীগুলি সমুদ্রের ভিতরে বহুধাবিভক্ত হয়ে এরূপ সঞ্চয় করতে থাকলে কালক্রমে পক্ষীপদসদৃশ ব-দ্বীপ বা পাখির পায়ের মত আকৃতির ব-দ্বীপ গড়ে ওঠে । বৈশিষ্ট্যঃ পক্ষীপদসদৃশ ব-দ্বীপ বা পাখির পায়ের মত ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – a) মোহনা অঞ্চলে অগভীর সমুদ্র ও নদীর স্রোত অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া (যাতে সমুদ্রের বেশ কিছুটা অভ্যন্তরে নদীপ্রবাহ প্রবেশ করতে পারে) এই প্রকার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য খুবই আবশ্যক । b) অধিকাংশক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম ও হালকা বালি, পলি, কাদামাটি, চুনাপাথর প্রভৃতি এই প্রকার ব-দ্বীপ গঠনের প্রধান উপাদান হিসাবে দেখা যায় । ৪. তীক্ষাগ্র ব-দ্বীপ বা কাসপেট ব-দ্বীপ (Cuspate Delta): ত্রিকোণাকার ব-দ্বীপের মধ্যভাগ বরাবর প্রবাহিত মূল নদীটি যদি ক্রমশ সমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে আরও প্রবেশ করতে থাকে তাহলে ঐ মূল নদীর দুই পাশে বাহিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণাকার ব-দ্বীপের অগ্রভাগ করাতের দাঁতের মত তীক্ষ্ণতা লাভ করে যে বিশেষ আকৃতির ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় তাকে তীক্ষাগ্র ব-দ্বীপ বা কাসপেট ব-দ্বীপ (Cuspate Delta) বলে । উদাঃ স্পেনের এব্রো ও ইটালির তাইবার নদীতে এইপ্রকার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে । বৈশিষ্ট্যঃ তীক্ষাগ্র ব-দ্বীপ বা কাসপেট ব-দ্বীপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – a) কাসপেট স্পিট থেকেই কালক্রমে এইপ্রকার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় । b) মোহনা অঞ্চলে অগভীর সমুদ্র ও নদীর স্রোত অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া (যাতে সমুদ্রের বেশ কিছুটা অভ্যন্তরে নদীপ্রবাহ প্রবেশ করতে পারে) এই প্রকার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য খুবই আবশ্যক । c) সমুদ্রতরঙ্গ ও জোয়ারভাটার ক্ষয়কার্যের প্রভাবে এইপ্রকার ব-দ্বীপের সম্মুখভাগ করাতের ধাঁরালো দাঁতের মত আকৃতি ধারণ করে । স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি (NATURAL LEVEE): ☻সংজ্ঞাঃ নদীর মধ্যপ্রবাহে ও বিশেষত নিম্নপ্রবাহে প্রায়শই পার্শ্ববর্তী দুকূলসংলগ্ন অঞ্চল বন্যার ফলে প্লাবিত হয় । কিছুদিন পর এই প্লাবনের জল সরে গেলে নদীবাহিত পলি, বালি, কর্দম প্রভৃতি নদীর দুই তীরে সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বাঁধের মত উঁচু হয়ে যায় । প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় বলে এই ধরনের বাঁধকে স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি (Natural Levee) বলে । উদাঃ গঙ্গা নদীর নিম্নপ্রবাহে তথা ভাগীরথী-হুগলী নদীর প্রবাহপথে, নীল নদের প্রবাহপথে স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি দেখা যায় । স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি (Natural Levee) উৎপত্তিঃ নদী তার নিম্নগতিতে সমুদ্রের কাছাকাছি চলে এলে ভূমির ঢাল হ্রাস পায় এবং নদীবাহিত সূক্ষ্ম কর্দম, পলি, বালি প্রভৃতি নদীগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে । ফলে নদীবক্ষ ভরাট হয়ে নদীর গভীরতা ক্রমশ কমে যায় । এমতাবস্থায়, বর্ষাকালে নদীতে হঠাৎ জল বেড়ে গেলে এই অগভীর উপত্যকা ছাপিয়ে নদীর দুই কূলের নীচু জমি প্লাবিত হয় । কিছুদিন পর এই প্লাবনের জল সরে গেলে নদীবাহিত পলি, বালি, কর্দম প্রভৃতি নদীর দুই তীরে সঞ্চিত হয় । এইভাবে ক্রমশ বছরের পর বছর নদীর তীরে এইরূপ সঞ্চয়ের ফলে ধীরে ধীরে বাঁধের মত উঁচু হয়ে যায় ও প্রাকৃতিকভাবে স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি সৃষ্টি হয় । বৈশিষ্ট্যঃ স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এগুলি প্রধানত নদীর ব-দ্বীপ প্রবাহেই উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে ওঠে । খ) এর উচ্চতা প্লাবনভূমির তল থেকে মোটামুটি ৩-৪ মিটার উঁচু হয় । গ) স্বাভাবিক বাঁধ বন্যা প্রতিরোধ করে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এরা সাময়িকভাবে বন্যা প্রতিরোধ করলেও তা কখনই চিরস্থায়ী ব্যবস্থারূপে গণ্য হয় না । কারণ নদীগর্ভে পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে অচিরেই আবার ভরাট হয়ে যায় এবং নদীতে পুনরায় বন্যা সৃষ্টি হয় । ঘ) এরা নদীপথের সমান্তরালে গড়ে ওঠে । এবিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন, মন্থর গতিসম্পন্ন কোনো নদীর স্বাভাবিক বাঁধ বন্যা প্রতিরোধের জন্য কৃত্রিম উপায়ে আরও উঁচু করা হয়, তা হলে ঐ নদীর দিকে ধাবমান কোনো উপনদী এই বাঁধের কারণে সহজে মূল নদীর সাথে মিলিত হতে পারে না । মূলনদীর সমান্তরালে তা বহুদূর অগ্রসর হয়ে অবশেষে উপযূক্ত স্থানে মূলনদীর সাথে মিলিত হয় । এইপ্রকার বিশেষ নদী-সঙ্গমকে বিলম্বিত সঙ্গম (Deferred Junction) বলে । উদাঃ মিসিসিপির উপনদী ইয়াজো (Yazoo) এইভাবে প্রায় ২৮০ কিলোমিটার পথ মিসিসিপির সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে মিলিত হয়েছে । ইয়াজো নদীর নামানুসারে এইরূপ সঙ্গমকে ইয়াজো জাতীয় সঙ্গমও (Yazootype Junction) বলা হয় । বিহারে পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যে এরকম বহু ইয়াজো জাতীয় নদীসঙ্গম গঙ্গার উভয় তীরে মিলিত হতে দেখা যায় । প্লাবনভূমি (FLOOD PLAIN): ☻সংজ্ঞাঃ নিম্নপ্রবাহে প্রায়ই প্লাবনের ফলে নদীর দুই কূল ভেসে জলে ডুবে যায় এবং তাতে পলি সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ যে পলিগঠিত সমভূমি সৃষ্টি হয়, তাকে প্লাবনভূমি (Flood Plain) বলে । উদাঃ ভাগীরথী-হুগলী (গঙ্গা), নীল, ইয়াং সিকিয়াং প্রভৃতি নদ-নদীর নিম্নপ্রবাহ জুড়ে বহু প্লাবনভূমি রয়েছে । প্লাবনভূমি (Flood Plain) উৎপত্তিঃ নদী তার নিম্নগতিতে সমুদ্রের কাছাকাছি চলে এলে ভূমির ঢাল হ্রাস পায় এবং নদীবাহিত সূক্ষ্ম কর্দম, পলি, বালি প্রভৃতি নদীগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে । ফলে নদীবক্ষ ভরাট হয়ে নদীর গভীরতা ক্রমশ কমে যায় । এমতাবস্থায়, বর্ষাকালে নদীতে হঠাৎ জল বেড়ে গেলে এই অগভীর উপত্যকা ছাপিয়ে নদীর দুই কূলের নীচু জমি প্লাবিত হয় । এভাবে বছরের পর বছর ধরে প্লাবিত অঞ্চলে নদীবাহিত পলি, বালি, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে ক্রমশ প্লাবনভূমি সৃষ্টি হয় । বৈশিষ্ট্যঃ প্লাবনভূমি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) বছরের পর বছর ধরে প্লাবনের ফলে প্লাবনভূমি সৃষ্টি হয়; এমনকি গঠনের কয়েক বছর পরেও এটি পুনরায় প্লাবিত হতে পারে । খ) এটি মোটামুটি সমতল প্রকৃতির হয় । গ) এটি খুবই উর্ব্বর প্রকৃতির হয় । ঘ) প্লাবনভূমি দৈর্ঘ্যে মোটামুটি ৩০-৬০ কিমি এবং প্রস্থে কয়েক মিটার থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে । নদীচড়া (SAND BANK): ☻সংজ্ঞাঃ নিম্নগতিতে নদীবক্ষে বালি, পলি, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে স্থানবিশেষে নদীবক্ষ ভরাট হয়ে জলতলের উপরে জেগে উঠলে সেই সাময়িক স্থলভাগকে নদীচড়া (Sand Bank) বলে । উদাঃ ভাগীরথী – হুগলী নদীর ব-দ্বীপ প্রবাহে নদীবক্ষে অনেক নদীচড়া দেখা যায় । নদী চড়া (Sand Bank) উৎপত্তিঃ নিম্নগতিতে নদীর স্রোতের বেগ কমে আসায় সঞ্চয় কার্যই প্রাধান্য পায় । এই অবস্থায় নদী অসম্ভব আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলে । এই নদীবাঁকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলধারা দুই তীরে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং নদী তার সাথে বয়ে আনা বালি, পলি, কর্দম প্রভৃতি আর বইতে না পেরে নদীগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে । এভাবে ক্রমশ নদীবক্ষ ভরাট হতে থাকে ও স্থানবিশেষে তা পরিনতিপ্রাপ্ত হয়ে অনেকসময় নদীর জলতলের উপরে নদীচড়ারূপে জেগে ওঠে । বৈশিষ্ট্যঃ নদীচড়া – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এগুলি মূলত নিম্নগতিতে সৃষ্টি হলেও অনেকসময় মধ্যগতিতেও দেখা যায় । খ) নদীর স্রোত, বাহিত বোঝার পরিমান ও প্রকৃতি প্রভৃতির উপর নদীচড়ার অবস্থান ও আকৃতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল । গ) নদীগর্ভে সর্বত্রই নদীচড়া সৃষ্টি হয় না, বিশেষত যেখানে নদীস্রোত কম সেখানেই নদীচড়া গড়ে ওঠে । ঘ) পাশাপাশি এবং পরপর অনেকগুলি নদীচড়া অবস্থানের ফলে নদী বিনুনীর মত আকৃতিতে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয় । একে বিনুনী নদী (Braided River) বলে । ঙ) সময়ের সাথে সাথে নদীচড়ার আকৃতি ও অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে । অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ( OX-BOW LAKE): ☻সংজ্ঞাঃ সমভূমি প্রবাহ ও ব-দ্বীপ প্রবাহে নদী বড় বড় বাঁক নিয়ে অগ্রসর হয় । বিশেষক্ষেত্রে এই প্রকার কোনো নদীবাঁক মূল নদীপ্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল নদীর পাশে অশ্ব বা ঘোড়ার ক্ষুরের মত আকৃতিতে অবস্থান করলে, তাকে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ( Ox-bow Lake) বলে । উদাঃ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী নদীর প্রবাহপথের পাশে এরকম অনেক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায় । উৎপত্তিঃ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ মূলতঃ তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় । যথা – ক) প্রথম পর্যায়ঃ পার্বত্য প্রবাহের পর নদী সমভূমি প্রবাহে ও ব-দ্বীপ প্রবাহে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পায় । এমতাবস্থায়, প্রবাহপথে নদী কোনো বড় বাঁধার সম্মুখীন হলে অথবা নদীখাতে সঞ্চয়ের ফলে বিশাল চর সৃষ্টি হলে নদী অস্বাভাবিক সর্পিলাকার আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হতে থাকে । খ) দ্বিতীয় পর্যায়ঃ নদীর এই সর্পিলাকার প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয় বিশাল বিশাল নদীবাঁক । এই নদীবাঁকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর জলধারা দুই তীরে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় । নদীর অবতল তীরে অর্থাৎ, বাঁক ঘোরার সময় নদীর যে স্থান সোতের ঠিক সম্মুখে থাকে সেখানে জলস্রোত ক্ষয় করে । ফলে ঐ স্থান ক্রমশ ভাঙতে থাকে । অপরদিকে, বিপরীততীরে অর্থাৎ উত্তল তীরে স্রোতের আঘাত বিশেষ না থাকার ফলে কিছু সঞ্চয় হতে থাকে । এইভাবে ক্রমান্বয়ে নদীর বাঁক ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং বাঁকের মধ্যবর্তী স্থান সংকীর্ণ হতে থাকে । এবং গ) তৃতীয় পর্যায়ঃ কালক্রমে এই সামান্য ব্যবধানও অবশেষে লুপ্ত হয় এবং নদী তার পুরোনো প্রবাহ ত্যাগ করে সোজা পথে প্রবাহিত হতে শুরু করলে নদীবাঁকের এই অংশ প্রধান নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার পাশে অবস্থান করে । এই বিচ্ছিন্ন অংশের সাথে প্রথমদিকে মূল নদীর সম্পর্ক থাকে এবং বন্যার সময় এই হ্রদে নদীর জল প্রবেশ করে । কিন্তু, সময়ের সাথে সাথে এক পর্যায়ে এই হ্রদ প্রধান নদী থেকে সম্পুর্ণ আলাদা হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্রভাবে (ঘোড়ার ক্ষুরের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকারে) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ রূপে অবস্থান করে । বৈশিষ্ট্যঃ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ – ক) সময়ের সাথে সাথে এটি ক্রমশ একটি মজে যাওয়া জলাভূমিতে পরিনত হয় । খ) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি ও তা পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে নদী তার আঁকাবাঁকা পথ ছেড়ে কিছুটা সোজা পথে অগ্রসর হয় । গ) এটি মূলত নিম্নপ্রবাহে দেখা গেলেও অনেকসময় নদীর মধ্যপ্রবাহেও সৃষ্টি হতে পারে । নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার (MEANDER): ☻বুৎপত্তিঃ ‘Meander’ শব্দটি এসেছে তুরস্কের বাঁকবহুল নদী মিয়েন্ড্রস (Maiandros) থেকে । সংজ্ঞাঃ পার্বত্য প্রবাহে নদীর জলস্রোতের গতি হ্রাস পায় ও নদী তার প্রবাহপথে অবস্থিত বাঁধাগুলিকে এড়িয়ে চলবার জন্য বড় বড় বাঁক নিয়ে এঁকেবেঁকে অগ্রসর হয় । এই বড় বড় বাঁকগুলিকে নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার (Meander) বলে । নদী বাঁক বা মিয়েন্ডার (Meander) উদাঃ ভারতের অধিকাংশ নদীগুলিতেই মিয়েন্ডার দেখতে পাওয়া যায় । উত্তরপ্রদেশের বারানসীর কাছে গঙ্গা নদীর গতিপথে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলংগীর মধ্যে নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার দেখা যায় । উৎপত্তিঃ পার্বত্য প্রবাহ থেকে নদী যতই সমভূমির উপর দিয়ে অগ্রসর হয়, ততই নদীর নিম্নক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় অধিক হওয়ার ফলে তার উপত্যকা চওড়া হতে থাকে । এমতাবস্থায়, নদীর জলস্রোতের গতিশক্তি ক্রমশ কমে যেতে থাকে । এর ফলে নদী তার প্রবাহপথে কোন বড় বাঁধার সম্মুখীন হলে নদী সেটি অতিক্রম করার পরিবর্তে বড় বড় বাঁক নিয়ে এড়িয়ে চলে । নদীর এই বাঁকে জলস্রোত এসে সর্বপ্রথম অবতল (Concave) ঢালে বা বাঁকের বাইরের দিকে আঘাত করে । এর ফলে সেখানে ক্ষয়কার্য দ্রুত হয় ও নদীর পাড় যথেষ্ট খাঁড়া হয় । অপরদিকে, উত্তল (Convex) ঢালে বা ভিতরের দিকে জলস্রোত অল্প থাকায় ক্ষয়কার্য বিশেষ হয় না উপরন্তু কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্য সেথায় জমা হতে থাকে । এভাবে ক্রমশ বাঁকের উত্তল ঢাল ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং অবতল ঢাল ক্রমশ আরও ঢালু হতে থাকে । ফলস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে উক্ত বাঁকগুলি আরও বৃহৎ রূপ নিতে থাকে এবং নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার (Meander) সৃষ্টি হয় । বৈশিষ্ট্যঃ নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এর একদিকে খাঁড়া পাড় ও অপরদিকে ঢালু পাড় থাকে । খ) এর খাঁড়া পাড়ের দিকে সাধারণত নদীখাত গভীর হয় । গ) নদী বাঁক বা মিয়েন্ডার থেকেই পরবর্তীতে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি হয় । ঘ) নদীর গতি ও নদীগর্ভের বোঝার সাথে নদীবাঁকের বিস্তারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । বায়ুর কাজ বালি তরঙ্গ (SAND RIPPLE),বালি শিরা (SAND RIDGE) ও বালি পাত (SAND SHEET): ☻বালি তরঙ্গ (Sand Ripple): মরু অঞ্চলে ঈষৎ অসমতল অংশে মৃদু বায়ুপ্রবাহ দ্বারা পরপর ঢেউ – এর ন্যায় আকৃতিতে যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়, তাকে বালি তরঙ্গ (Sand Ripple) বলে । উদাঃ সাহারা মরুভূমিতে বালি তরঙ্গ দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ বালি তরঙ্গ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) বালিরাশির লম্ফদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বালি তরঙ্গ সৃষ্টি হয় । খ) এর অনুবাত ঢালের তুলনায় প্রতিবাত ঢাল বেশি উঁচু হয় । ☻বালি শিরা (Sand Ridge): মরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহজনিত সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট বাঁধের ন্যায় ভূমিরূপকে বালি শিরা (Sand Ridge) বলে । উদাঃ থর মরুভূমিতে বালি শিরা দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ বালি শিরা – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এরা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ কিমি, প্রস্থে ১-৩ কিমি ও উচ্চতায় ৫০ মিটারের আশেপাশে হয় । খ) এরা বায়ুপ্রবাহের গতিপথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে । ☻বালি পাত (Sand Sheet): মরু অঞ্চলে অত্যন্ত সমতল অংশে বায়ুপ্রবাহবাহিত বালি জমতে থাকলে একটি পাতলা বালির স্তর তৈরী হয় । একে বালি পাত (Sand Sheet) বলে । উদাঃ লিবিয়ার ‘সেলিমা’ নামক বালি পাত । বৈশিষ্ট্যঃ বালি পাত – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এগুলি মরু অঞ্চলের প্রসারণে সাহায্য করে । খ) এরা খুব পাতলা প্রকৃতির হয় । লোয়েস সমভূমি (LOESS PLAIN): ☻বুৎপত্তিগত অর্থঃ ‘Loess’ শব্দটি জার্মান শব্দ ‘Loss’ থেকে এসেছে, যার অর্থ “সূক্ষ্ম পলি”। সংজ্ঞাঃ অতিসূক্ষ্ম বালিকণা বায়ুপ্রবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে মরুভূমি সীমানার অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে জমা হয়ে যে সমভূমি গঠন করে, তাকে লোয়েস সমভূমি (Loess Plain) বলে । বিশিষ্ট জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী রিকটোফেন (Richthofen) সর্বপ্রথম লোয়েস চিহ্নিত করেন । উদাঃ মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমি থেকে বালিরাশি শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুবাহিত হয়ে উত্তর চিনের হোয়াংহো নদীর অববাহিকায় দীর্ঘদিন ধরে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে সেখানে এক বিস্তীর্ণ ও উর্বর লোয়েস সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে । অবস্থানঃ পৃথিবীতে মূলতঃ চারটি লোয়েস সমভূমি অঞ্চল দেখা যায় । যথা – ক) এশিয়ার লোয়েস অঞ্চলঃ এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম চীনে ৬৪৫ হাজার বর্গকিলোমিটারব্যাপী এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি অবস্থিত । উত্তর-পশ্চিম চীনব্যতীত মধ্য-এশিয়ার আরও বিভিন্ন অববাহিকায় লোয়েস দেখতে পাওয়া যায় । খ) ইউরোপের লোয়েস অঞ্চলঃ মধ্য ইউরোপের উচ্চভূমির উত্তরে জার্মানীর বোর্দি (Borde) নামক অঞ্চলে; মধ্য বেলজিয়ামের নিম্ন-মালভূমি ও ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বাংশে লোয়েস সঞ্চয় দেখা যায় । গ) উত্তর আমেরিকার লোয়েস অঞ্চলঃ উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরী নদী উপত্যকা অঞ্চলে লোয়েস সঞ্চয় দেখা যায় । ইলিনয়, আইওয়া এবং নেব্রাস্কার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল লোয়েস দ্বারা আবৃত । এবং ঘ) দক্ষিন আমেরিকার লোয়েস অঞ্চলঃ লোয়েস অবক্ষেপ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পম্পাসেও দেখতে পাওয়া যায় । বৈশিষ্ট্যঃ লোয়েস সমভূমি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এর রং হলদে । খ) এটি অতি সুক্ষ্ম নরম, প্রবেশ্য ও চুনময় । গ) এই মাটি খুবই উর্বর । ঘ) এটি পলি দ্বারা গঠিত,যার মধ্যে কোণবিশিষ্ট কোয়ার্টজ, ফেলসপার, ক্যালসাইট, ডলোমাইট এবং অন্যান্য খনিজের কণা একত্রে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে । ঙ) এই মৃত্তিকার প্রস্থচ্ছেদ করলে অসংখ্য উল্লম্ব সরু নল বা টিউবের ন্যায় ছিদ্রপথের অবস্থান দেখা যায় । চ) এর সূক্ষ্ম কণাগুলি পরস্পরের সাথে সুসংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে । ছ) লোয়েসের মধ্যবর্তী অসংখ্য ছিদ্রপথ থাকায় এর মধ্য দিয়ে জল সহজেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি (ADVANCED DUNE) ও পরবর্তী বালিয়াড়ি (WAKE DUNE): ☻ অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি (Advanced Dune): অনেক সময় ঘূর্ণি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে মস্তক বালিয়াড়ির কিছুটা আগে অপর একপ্রকার বালিয়াড়ি সৃষ্টিহয় । একে অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি (Advanced Dune) বলে । উদাঃ থর মরুভূমিতে অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এইপ্রকার বালিয়াড়ি আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় । খ) এরা দেখতে স্তূপাকৃতি হয় । ☻ পরবর্তী বালিয়াড়ি (Wake Dune): পুচ্ছ বালিয়াড়ির পরবর্তী পর্যায়ে যে বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়, তাকে পরবর্তী বালিয়াড়ি (Wake Dune) বলে । উদাঃ থর মরুভূমিতে পরবর্তী বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ পরবর্তী বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এইপ্রকার বালিয়াড়ি আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় । খ) এরা দেখতে ক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি হয় । মস্তক বালিয়াড়ি (HEAD DUNE),পুচ্ছ বালিয়াড়ি (TAIL DUNE) ও পার্শ্ব বালিয়াড়ি (LATERAL DUNE): ☻মস্তক বালিয়াড়ি (Head Dune): বায়ুপ্রবাহ তার গতিপথে কোন বাঁধার সম্মুখীন হলে সেই বাঁধার প্রতিবাত অংশে যে বালিয়াড়ি গড়ে ওঠে, তাকে মস্তক বালিয়াড়ি (Head Dune) বলে । উদাঃ থর মরুভূমিতে মস্তক বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ মস্তক বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এরা আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় । খ) এরা অনেকটা পাখির ঠোঁটের মত আকৃতিবিশিষ্ট হয় । ☻পুচ্ছ বালিয়াড়ি (Tail Dune): বায়ুপ্রবাহ তার গতিপথে কোন বাঁধার সম্মুখীন হলে সেই বাঁধার পিছনদিকেও অল্প পরিমানে বালি পরিবাহিত হয় এবং তা ঐ স্থানে থিঁতিয়ে পড়ে বালিয়াড়ি সৃষ্টি হলে, তাকে পুচ্ছ বালিয়াড়ি (Tail Dune) বলে । উদাঃ থর মরুভূমিতে পুচ্ছ বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ পুচ্ছ বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এরা আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় । খ) এরা দেখতে স্তূপাকৃতি হয় । ☻পার্শ্ব বালিয়াড়ি (Lateral Dune):বায়ুপ্রবাহ তার প্রবাহপথে বাঁধার সম্মুখীন হলে বাঁধার দু পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় । এর ফলে বাঁধার দুই পাশে বালি থিঁতিয়ে পড়ে যে বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়,তাকে পার্শ্ব বালিয়াড়ি (Lateral Dune) বলে । উদাঃ থর মরুভূমিতে পার্শ্ব বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ পার্শ্ব বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এরা আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় । খ) এরা দেখতে দণ্ডাকৃতি হয় । চুলের কাঁটার ন্যায় বালিয়াড়ি (HAIRPIN DUNE): ☻সংজ্ঞাঃ অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি প্রসারিত হতে হতে দীর্ঘ, সংকীর্ণ ও সমান্তরাল ঢালযুক্ত বালিয়াড়ি সৃষ্টি হলে, তাকে চুলের কাঁটার ন্যায় বালিয়াড়ি (Hairpin Dune) বলে । উদাঃ আফ্রিকার নামিবিয়া মরুভূমিতে চুলের কাঁটার ন্যায় বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ চুলের কাঁটার ন্যায় বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি থেকে এইপ্রকার বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয় । খ) কখনও কখনও এগুলির উপর উদ্ভিদ জন্মালে এরা স্থির বালিয়াড়িতে পরিণত হয় । উল্টানো বালিয়াড়ি (REVERSE DUNE): ☻সংজ্ঞাঃ প্রাথমিক ঢালের ঠিক বিপরীত দিকে সৃষ্ট অপ্রধান ঢালযুক্ত শৈলশিরার মতো আকৃতিবিশিষ্ট বালিয়াড়ি উল্টানো বালিয়াড়ি (Reverse Dune) নামে পরিচিত । উদাঃ কালাহারি মরুভূমিতে প্রচুর সংখ্যক উল্টানো বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ উল্টানো বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এইপ্রকার বালিয়াড়ি বায়ুপ্রবাহের পথে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে । খ) তীর্যক বালিয়াড়ি ও বার্খান – এই দুই বালিয়াড়ির মধ্যে এদের অবস্থান দেখা যায় । গ) দুটি সমশক্তিসম্পন্ন বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের স্থায়িত্বকাল সমান হলে এরূপ বালিয়াড়ি গড়ে ওঠে । দ্রাস বালিয়াড়ি (DRUSH DUNE): ☻সংজ্ঞাঃ তিমি মাছের পৃষ্ঠদেশের মতো সমতল শিখরবিশিষ্ট বালিয়াড়িকে দ্রাস বালিয়াড়ি (Drush Dune) বা তিমিপৃষ্ঠ বালিয়াড়ি (Whaleback Dune) বলে । উদাঃ সাহারা মরুভূমিতে দ্রাস বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ দ্রাস বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এগুলি বায়ু্প্রবাহের গতিপথের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে । খ) এইপ্রকার বালিয়াড়ি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ কিমি, প্রস্থে ১-৩ কিমি ও উচ্চতায় প্রায় ৪০০ মিটার পর্যন্ত হয় । অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি (PARABOLIC DUNE): ☻সংজ্ঞাঃ মরুভূমি অঞ্চলে বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট গর্তগুলির প্রতিবাত ঢাল থেকে বালি অপসারিত হয়ে অনুবাত ঢালে সঞ্চিত হয়ে অধিবৃত্তের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বালিয়াড়ি সৃষ্টি হলে, তাকে অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি (Parabolic Dune) বলে । উদাঃ আফ্রিকার নামিবিয়া মরুভূমিতে অনেক অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ অধিবৃত্তীয় বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এইপ্রকার বালিয়াড়ি বেলচা বা চামচের গর্তের মত আকৃতিবিশিষ্ট হয় । খ) এর প্রতিবাত ঢাল অনুবাত ঢালের থেকে কম হয় । অ্যাকলি বালিয়াড়ি (ALKLE DUNE): ☻সংজ্ঞাঃ অনেকগুলি বার্খান বালিয়াড়ি পরস্পরযুক্ত হয়ে দীর্ঘ সাপের দেহের মতো আকৃতিতে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করলে, তাকে অ্যাকলি বালিয়াড়ি (Alkle Dune) বলে । অ্যাকলি বালিয়াড়ি (Alkle Dune) উদাঃ সাহারা মরুভূমিতে অ্যাকলি বালিয়াড়ি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ অ্যাকলি বালিয়াড়ি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) বছরে দুটি নির্দিষ্ট সময়ে দুটি নির্দিষ্ট দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে এইপ্রকার বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয় । খ) অ্যাকলি বালিয়াড়ির এগিয়ে যাওয়া বাঁকটিকে লিঙ্গুঅয়েড ও পিছিয়ে যাওয়া বাঁকটিকে বার্খানঅয়েড বলে । বায়ু ও জলের মিলিত কাজ বায়ুপ্রবাহ ও জলধারার মিলিত কার্য ও সৃষ্ট ভুমিরূপগুলি(LANDFORMS FORMED DUE TO THE COMBINED WORK OF WIND AND WATER): ☻ সাধারনতঃ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে মরুভূমিগুলি সৃষ্টি হলেও মরু অঞ্চলগুলি কিন্তু একেবারেই বৃষ্টিহীন নয় । মাঝে মাঝেই মরু অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেও তা আকস্মিক ও মুষলধারে ঘটে । এর ফলে ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু বেগবান ও ক্ষণস্থায়ী জলধারার সৃষ্টি হয় । এই জলধারাগুলি ভূমির ঢাল অনুসারে প্রবাহিত হয়ে বালি, পলি, কাঁকর, সুক্ষ্ম শিলাচূর্ণ প্রভৃতি মিশে প্রবল বেগে নিচে নেমে আসে । এই জলধারা ও বায়ুপ্রবাহের মিলিত কার্যের ফলে মরু অঞ্চলে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় । এগুলি হলো – ক) পেডিমেন্ট (Piedmont), খ) বাজাদা (Bajada), গ) ওয়াদি (Wadi), ঘ) প্লায়া (Playa) প্রভৃতি । মরুদ্যান (OASIS) : ☻ সংজ্ঞাঃ মরু অঞ্চলে বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে কোন একটি অঞ্চলের বালিরাশি অপসারিত হতে থাকলে অঞ্চলটি ক্রমশ অবনমিত হয়ে পড়তে পড়তে একসময় ভৌমজলস্তর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । ফলে ওই স্থানে জলাশয় সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ উদ্ভিদ জন্মে অঞ্চলটিতে মনোরম পরিবেশ তৈরী হয় । শুষ্ক মরু অঞ্চলের মধ্যে এরকম সবুজাভ স্থানকে মরুদ্দ্যান (Oasis) বলে । উদাঃ সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ একটি আদর্শ মরুদ্দ্যান । বৈশিষ্ট্যঃ মরুদ্দ্যান – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) একে কেন্দ্র করে ক্রমশ ঐ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠে । খ) এগুলি শুষ্ক মরুভূমির মাঝে একমাত্র আশ্রয়স্থল । প্লায়া (PLAYA): ☻ বুৎপত্তিগত অর্থঃ ‘Playa’ একটি স্প্যানিশ শব্দ, যার অর্থ “লবনাক্ত হ্রদ” । সংজ্ঞাঃ মরুভূমিতে পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলের ভিতরে সৃষ্ট লবনাক্ত হ্রদকে প্লায়া (Playa) বলে । এটি আফ্রিকায় শটস, মেক্সিকোতে বোলসন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্যালিনা নামে পরিচিত । উদাঃ রাজস্থানের সম্বর হ্রদ একটি আদর্শ প্লায়া । বৈশিষ্ট্যঃ প্লায়া – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এর আয়তন কয়েক বর্গ মিটার থেকে কয়েক কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে । খ) এর উপরিভাগে চকচকে লবনের স্তর থাকে । ওয়াদি (WADI): ☻ বুৎপত্তিগত অর্থঃ ‘ওয়াদি’ একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ হল ‘শুষ্ক উপত্যকা’ । সংজ্ঞাঃ মরু অঞ্চলে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে সাময়িক জলধারার সৃষ্টি হয় । এই জলধারার সাথে বালি, কাঁকর, কাদা প্রভৃতি কর্দমধারা রূপে প্রবাহিত হয়; কিন্তু খুব দ্রুত এই কর্দমধারার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ও নদীখাত শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকে । মরু অঞ্চলে অবস্থিত এরকম শুষ্ক নদীখাতগুলি ওয়াদি(Wadi) নামে পরিচিত । উদাঃ আরবে ‘রাব-আল-খালি’ মরুভূমিতে ওয়াদি দেখা যায় । ওয়াদি (Wadi) উৎপত্তিঃ সাধারনত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে মরুভূমিগুলি সৃষ্টি হলেও মরু অঞ্চলগুলি কিন্তু একেবারেই বৃষ্টিহীন নয় । মাঝে মাঝেই মরু অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয় (বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫-৪৮ সেন্টিমিটার) । কিন্তু সেই বৃষ্টিপাত পরিমানে সামান্য হলেও তা স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিক ও মুষলধারে ঘটে । এর ফলে ঐ অঞ্চলে বেশকিছু বেগবান ও ক্ষণস্থায়ী জলধারার সৃষ্টি হয় । এই জলধারা ভূমির ঢাল অনুসারে প্রবাহিত হয়ে বালি, পলি, কাঁকর, সুক্ষ্ম শিলাচূর্ণ প্রভৃতি মিশে একটি কর্দম ধারা রূপে প্রবল বেগে নিচে নেমে আসে । কিন্তু প্রবাহপথে জলের দ্রুত অধঃগমন ও অধিক পরিমানে বাস্পীভবনের কারণে নদীখাতটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গিয়ে ওয়াদি সৃষ্টি হয় । বৈশিষ্ট্যঃ ওয়াদি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – (ক) এটি স্বল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয় । (খ) বছরের অধিকাংশ সময় এটি শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকে । (গ) বালি, পলি, কাঁকর ও বিভিন্ন আকৃতির শিলাচূর্ণ দ্বারা এর তলদেশ ভরাট থাকে । পেডিমেন্ট (PIEDMONT) ও বাজাদা (BAJADA): ☻পেডিমেন্ট (Piedmont): বুৎপত্তিগত অর্থঃ ‘Pedi’ শব্দের অর্থ ‘পাদদেশ’ ও ‘Mont’ শব্দের অর্থ ‘পাহাড়’ । সংজ্ঞাঃ মরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে পাহাড়ের পাদদেশে গঠিত শিলাময়, মৃদু ঢালযুক্ত, প্রায় সমতল ভূমিকে পেডিমেন্ট(Piedmont) বলে । উদাঃ সাহারা মরুভূমিতে পাহাড়ের পাদদেশে পেডিমেন্ট দেখা যায় । পেডিমেন্ট (Piedmont) ও বাজাদা (Bajada) শ্রেণীবিভাগঃ পেডিমেন্ট মূলত তিন প্রকার । যথা- ১. লুক্কায়িত পেডিমেন্ট, ২. সমবেত পেডিমেন্ট ও ৩. ব্যবচ্ছিন্ন পেডিমেন্ট । বৈশিষ্ট্যঃ পেডিমেন্ট – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) পেডিমেন্টের উপরের দিকের ঢাল ৭° ও নিচের দিকের ঢাল ১° / ২° এর মত হয় । খ) এটি ছোট-বড় প্রস্তরখন্ড, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি দ্বারা গঠিত হয় । ☻বাজাদা (Bajada): বুৎপত্তিগত অর্থঃ ‘Bajada’ শব্দটি একটি স্প্যানিশ শব্দ ‘Bahada’ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘পাশাপাশি সৃষ্ট একাধিক পলি শঙ্কুগঠিত সমভূমি’ । সংজ্ঞাঃ পেডিমেন্টের নিচের অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা বাহিত হয়ে সুক্ষ্ম বালি, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে প্রায় সমভূমির ন্যায় ভুমিরূপ সৃষ্টি হয়, তাকে বাজাদা (Bajada) বলে । উদাঃ সাহারা মরুভূমিতে পাহাড়ের পাদদেশে পেডিমেন্টের সাথে বাজাদা দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ বাজাদা – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এটি পেডিমেন্টের পরবর্তী অংশ । খ) এর ঢাল অত্যন্ত কম (১/২° – ১°) । গ) অপেক্ষাকৃত সুক্ষ্ম বালি, পলি প্রভৃতি দ্বারা বাজাদা গঠিত হয় । হিমবাহের কাজ নুনাটকস (NUNATAKS): ☻বুৎপত্তিগত অর্থঃ ‘নুনাটকস’ একটি এস্কিমো ভাষার শব্দ, যার অর্থ ‘তুষারমুক্ত ভূমি’ । সংজ্ঞাঃ উপকূলস্থ মহাদেশীয় হিমবাহের গভীরতা কমে গেলে দেখা যায় তার মধ্যে কোন এক পর্বতের চুড়া মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে, কিন্তু তার চূড়ায় কোন বরফ নেই । বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী মহাদেশীয় হিমবাহ মধ্যস্থিত এরকম বরফবিহীন পর্বতের শিখরকে নুনাটকস (Nunataks) বলে । উদাঃ মাউন্ট তাকাহি হলো একটি আদর্শ নুনাটকস । বৈশিষ্ট্যঃ নুনাটকস – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এ্রর তলদেশ বরফাবৃত, কিন্তু শিখরদেশ বরফমুক্ত থাকে । খ) মূলতঃ মহাদেশীয় হিমবাহের মাঝে এটি দেখা যায় । নেভে (NEVE),ফির্ন (FIRN) ও বরফ (ICE): ☻নেভে(Neve): তুষারপাতের প্রাথমিক অবস্থায় তুষারকণাগুলি একটি অপরটির সাথে আলগাভাবে লেগে থাকে । এরকম ফাঁকযুক্ত আলগা তুষারকণাগুলিকে নেভে (Neve) বলে । বৈশিষ্ট্যঃ নেভে – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এগুলি অতি সূক্ষ্ম ও হালকা তুষারকণা । খ) এর ঘনত্ব ০.৬-০.১৬ গ্রাম / কিউবিক সেমি । ☻ ফির্ন (Firn): নেভের পরবর্তী রূপ হলো ফির্ন (Firn) । এগুলি এমন একপ্রকার তুষারকণা গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতায় সম্পূর্ণ গলে যায়, আবার পরবর্তী শীতে নানারকম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় । বৈশিষ্ট্যঃ ফির্ন – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এটি সাধারণভাবে অসংগঠিত হয় । খ) এর ঘনত্ব ০.৭২-০.৯ গ্রাম / কিউবিক সেমি । ☻ বরফ (Ice): সমগ্র তুষারকণা জমাট বেঁধে স্তূপের আকার নিলে তাকে বরফ (Ice) বলে । বৈশিষ্ট্যঃ বরফ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এটি সাধারণভাবে সংগঠিত হয় । খ) এর ঘনত্ব ০.৯ গ্রাম / কিউবিক সেমির বেশী হয় । এস্কার (ESKER) ও কেম (KAME): ☻ এস্কার (Esker): উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে হিমবাহের বহন করে আনা বিভিন্ন আকৃতির নুড়ি, পাথর, কাদা, বালি, কাঁকর প্রভৃতি জমা হয়ে দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা, নাতিউচ্চ ও সংকীর্ণ বাঁধের মতো শৈলশিরা বা উচ্চভূমি গঠন করে । একে এস্কার (Esker) বলে । উদাঃ ফিনল্যান্ডের পুনকাহারয়ু একটি বিখ্যাত এস্কার । বৈশিষ্ট্যঃ এস্কার – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এটি বহিঃবিধৌত সমভূমির মধ্যে অবস্থিত হয় । খ) হিমবাহ থাকাকালীন এটি দেখা যায় না, হিমবাহ গলে গেলে এটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । এস্কার (Esker) ও কেম (Kame) ☻ কেম (Kame): অনেক সময় পার্বত্য হিমবাহের শেষপ্রান্তে হিমবাহ যেখানে গলতে শুরু করে সেখানে কাদা, বালি, নুড়ি, পাথর, কাঁকর ইত্যাদি স্তূপাকারে সঞ্চিত হয়ে ব-দ্বীপআকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ত্রিকোণাকার যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়, তাকে কেম (Kame) বলে । উপত্যকার দুই পাশে কেম সৃষ্টি হলে তাকে কেমমঞ্চ বাকেমসোপান বলে । উদাঃ পূর্ব স্কটল্যান্ডের ল্যামারহিলে বহু কেম দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ কেম – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) কেম হলো হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । খ) এগুলি উপত্যকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে মিশে ধাপ তৈরি করে ড্রামলিন (DRUMLIN): ☻ বুৎপত্তিগত অর্থ: “Drumlin” শব্দটির অর্থ ‘ঢিবি’ । সংজ্ঞা: হিমবাহ গলে গেলে বহিবিধৌত সমভূমিতে স্তূপীকৃত বোল্ডার ক্লে অনেক সময়ে সারিবদ্ধ টিলা বা ছোটো ছোটো স্তূপের আকারে বিরাজ করে । ভূ-পৃষ্ঠের উপর এদের দেখতে অনেকটা উলটানো নৌকা বা চামচের মতো আকৃতির হয় । এদের ড্রামলিন (Drumlin) বলে । উদাঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল, উত্তর ইংল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে বহু ড্রামলিন দেখা যায় । ড্রামলিন (Drumlin) বৈশিষ্ট্যঃ ড্রামলিন – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) একটি আদর্শ ড্রামলিন ১-২ কি.মি. দীর্ঘ ৪০০-৬০০ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-৩০ মিটার উঁচু হয় । খ) ড্রামলিনের হিমবাহ প্রবাহের দিকটি অমসৃণ এবং বিপরীত দিকটি মসৃণ হয়ে থাকে । গ) একক ড্রামলিন সাধারণত দেখা যায় না, সাধারণত ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রামলিন দেখা যায় । ঘ) বহু ড্রামলিন একসঙ্গে অবস্থান করলে তাদের মধ্যবর্তী অবনত অঞ্চলগুলোতে জল জমে জলাভূমি সৃষ্টি হয় । ঙ) অনেক উঁচুজায়গা থেকে দেখলে ড্রামলিনগুলিকে ‘ডিম ভর্তি ঝুড়ি’ – র মত মনে হয় । ড্রামলিন অধ্যুষিত অঞ্চলকে তাই “Basket of Eggs Topography” বলে । হিমকর্দ বা বোল্ডার ক্লে (BOULDER CLAY): সংজ্ঞাঃ হিমবাহ গলে গেলে তার নীচে হিমবাহের সঙ্গে বয়ে আনা বালি ও কাদার সঙ্গে বিভিন্ন আকৃতির নুড়ি-পাথর অবক্ষেপ হিসাবে সঞ্চিত হলে, তাদের একসঙ্গে বোল্ডার ক্লে (Boulder Clay) বা হিমকর্দ বলা হয় । উদাঃ উত্তর ইউরোপের হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে বোল্ডার ক্লে দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ বোল্ডার ক্লে – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এটি বালি ও কর্দম মিশ্রিত বিভিন্ন আকৃতির শিলাখন্ডের একত্রিত সঞ্চয় । খ) এগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চিত হয় । আগামুক বা ইরাটিক (ERRATICS): ☻সংজ্ঞাঃ হিমবাহ উপর থেকে বিভিন্ন আকৃতির শিলাচূর্ণ একই সঙ্গে নিয়ে এসে এক জায়গায় জমা করে । এগুলিকে একত্রে অবক্ষেপ বলে । এই হিমবাহ অবক্ষেপের বড় বড় আকৃতির গোলাকার নুড়িপাথরগুলিকে আগামুক বা ইরাটিক (Erratics) বলে । উদাঃ কাশ্মীরের পহেলগামের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে আগামুক বা ইরাটিক দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ আগামুক বা ইরাটিক – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এগুলির সাথে আঞ্চলিক শিলাসমূহের আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত কোনো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না । খ) এগুলি আকৃতিতে বৃহৎ ও গোলাকার হয় । বহিঃবিধৌত সমভূমি (OUT-WASH-PLAIN): ☻সংজ্ঞাঃ উচ্চ পর্বতের পাদদেশে হিমবাহ এসে পৌঁছালে তা গলে নদীর সৃষ্টি হয় এবং সেখানে হিমবাহবাহিত পাথরের টুকরো, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাদা প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে বিস্তীর্ণ সমভূমি গঠন করে, তাকে বহিঃবিধৌত সমভূমি (Out-Wash-Plain) বলে । বহিঃবিধৌত সমভূমি (Out-Wash-Plain) উদাঃ কানাডার উত্তরাংশে বহিঃবিধৌত সমভূমি দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ বহিঃবিধৌত সমভূমি – র বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) এটি একটি বিশাল সমতলভূমি । খ) এর উপরে অসংখ্য ড্রামলিন দেখা যায় । অবক্ষেপ (DRIFT): ☻সংজ্ঞাঃ পর্বতের নিম্নাংশ ও নিম্নভূমিতে হিমবাহ প্রধানত অবক্ষেপণ করে থাকে । নদী যেমন তার বাহিত বস্তুগুলিকে যথা– নুড়ি, পাথর, কাদা, বালি, কাঁকর প্রভৃতি আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন অংশে সঞ্চয় করে, হিমবাহ তা করে না । হিমবাহ উপর থেকে বিভিন্ন আকৃতির শিলাচূর্ণ একই সঙ্গে নিয়ে এসেএক জায়গায় জমা করে, এগুলিকে একত্রে অবক্ষেপ (Drift) বলে । উদাঃ কানাডার উত্তরাংশে অবক্ষেপ দেখা যায় । বৈশিষ্ট্যঃ অবক্ষেপ – এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ – ক) মূলত পর্বতের নিম্নাংশে এটি দেখা যায় । খ) অবক্ষেপ হিমবাহবাহিত বিভিন্নপ্রকার আকৃতির শিলাচূর্ণ নিয়ে গড়ে ওঠে ।


Comments